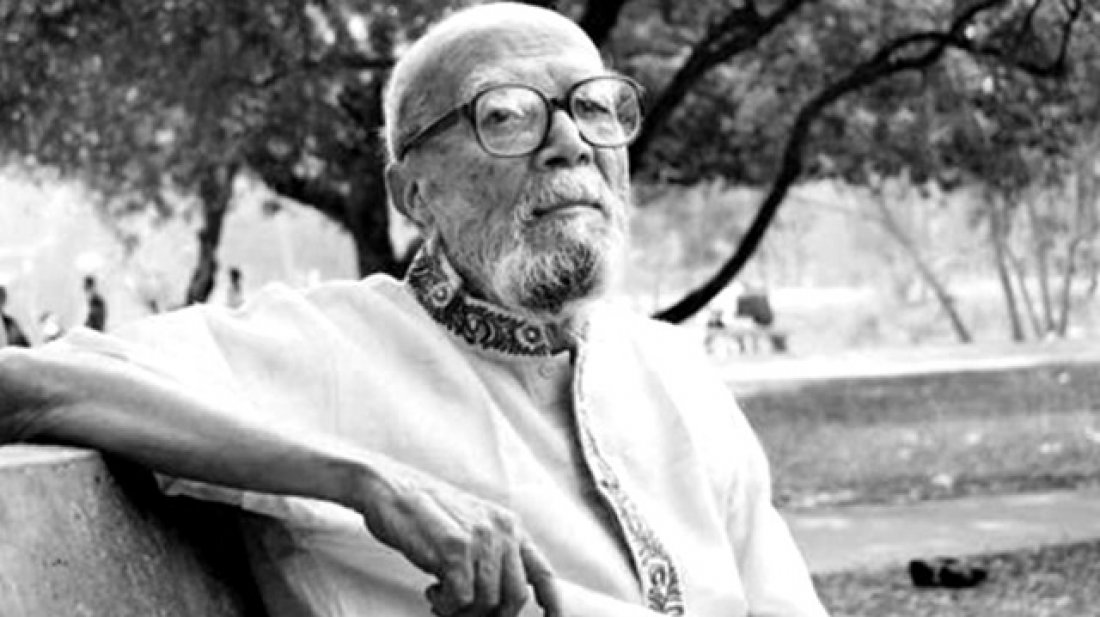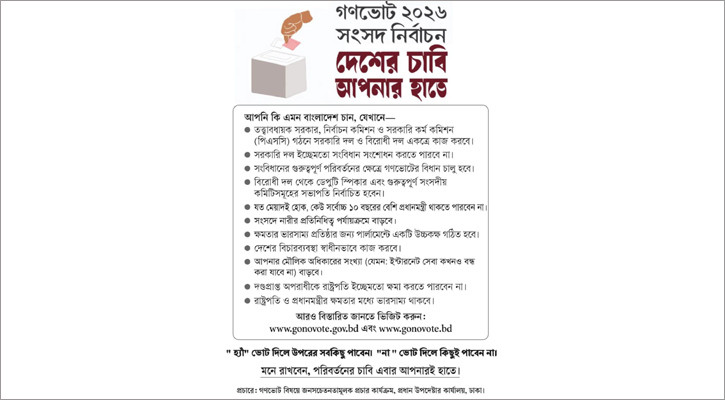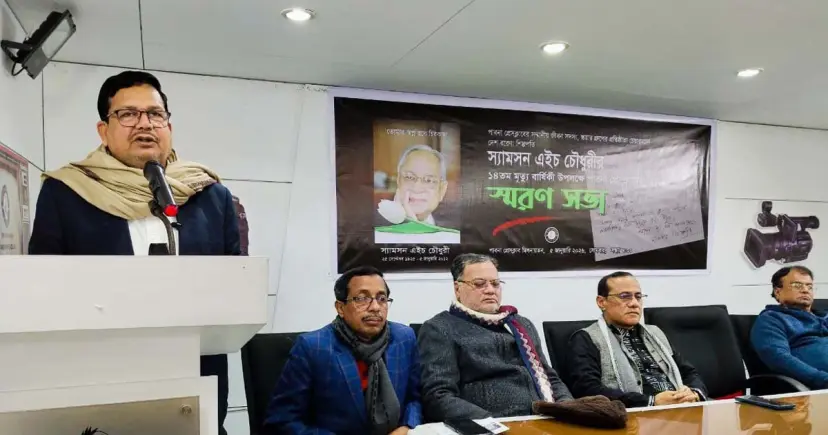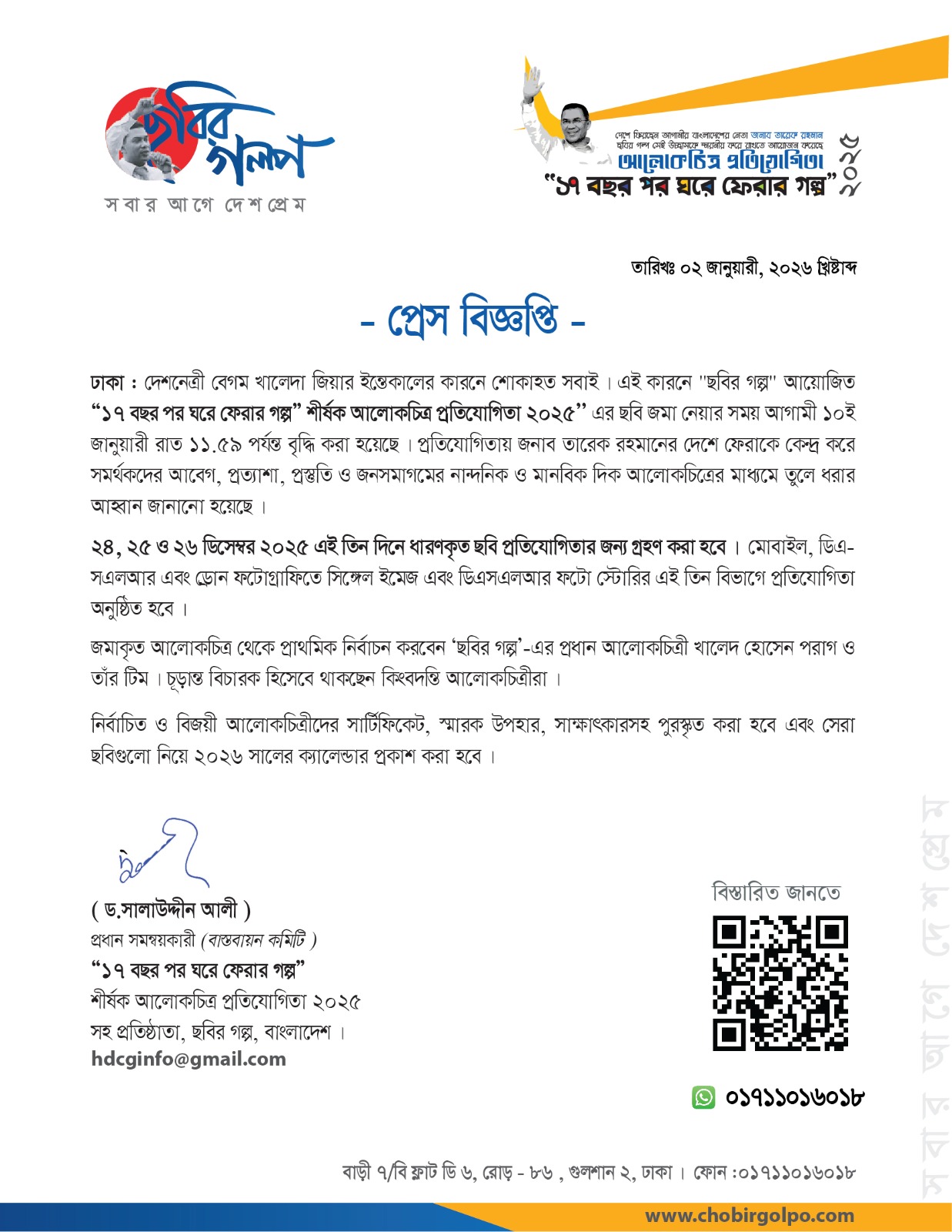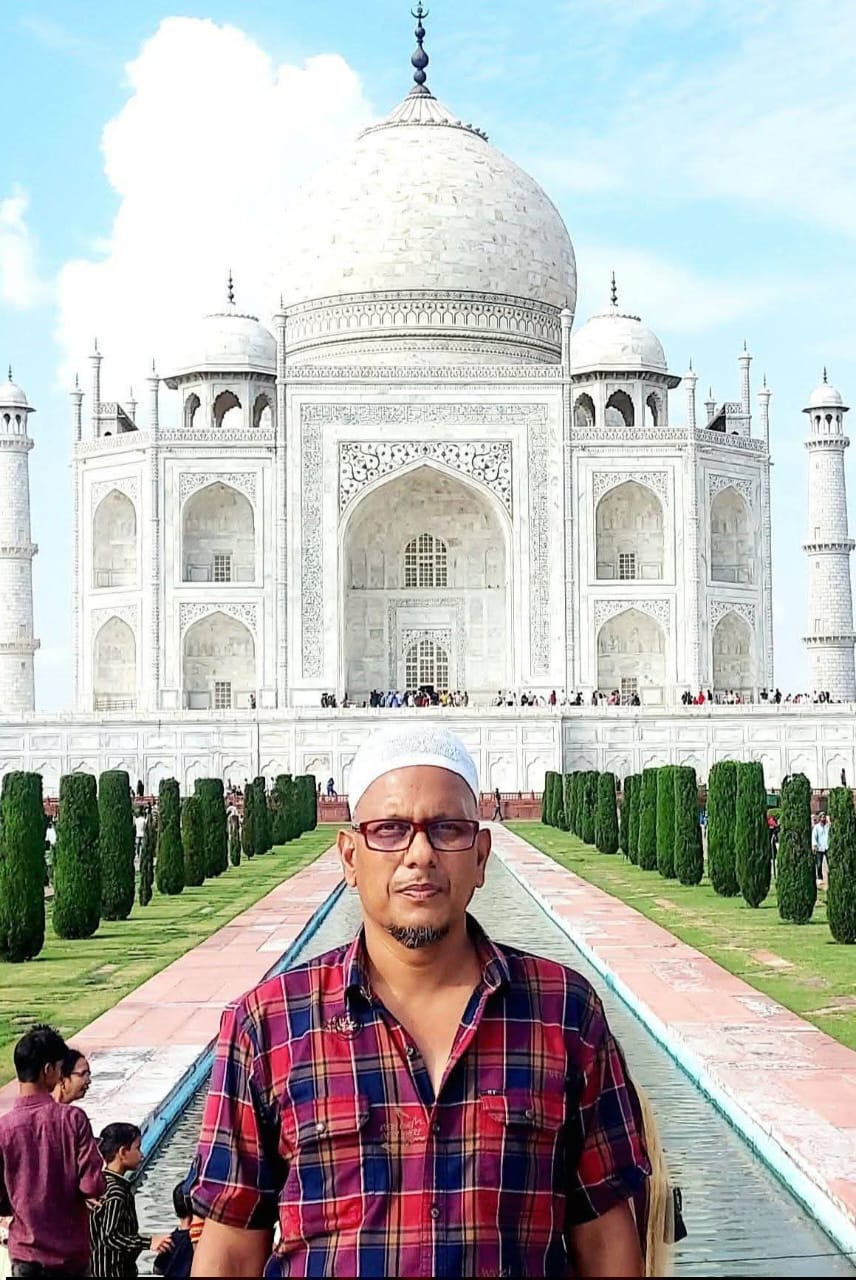আমাদের লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য আল মাহমুদের কবিতায় যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ভাষা-আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও তিনি লিখেছেন। বলা চলে, তিনি সময়কে এড়িয়ে যেতে চাননি, বরং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ গেঁথেছেন অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার বলে। তাঁর আগপর্যন্ত বাংলা কবিতার রাজধানী কলকাতাকে ভাবা হতো, কলকাতার কবিদের সমীহ করা হতো। তিনি আর শামসুর রাহমান বাংলা কবিতার রাজধানীর মর্যাদা কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন। জীবনের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ: লোক-লোকান্তর (১৯৬৩) এবং কালের কলস (১৯৬৬)। এই কবিতাগুলির বৃত্তে একটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে বাম ধারার দিকে ঝোঁকে পড়ার প্রবণতা। বাংলা কবিতায় তিনি যে ‘ধাক্কা দিতে যাচ্ছেন’ তা এখান থেকেই অনেক বোদ্ধা বুঝে নেন। তারপরেই প্রকাশিত হয় অমর কাব্য, আলোড়ন তোলা সোনালি কাবিন (১৯৭৩)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কাব্যগ্রন্থ তাঁর প্রথম এবং সব মিলিয়ে তৃতীয় গ্রন্থ। আগেই তিনি নিজেকে একজন উদীয়মান কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে, তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা কলকাতা ও ঢাকার আলোচিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে বাছাই বা প্রকাশিত হতে থাকে। বিশেষ করে কলকাতার কৃত্তিবাস ।বাংলাদেশের সমকাল পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় আল মাহমুদের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হওয়ায়।
“সর্প বিতানের কোনো ফলবান বৃক্ষের শিকড়ে
খুলে দিয়ে দুটি উষ্ণ উরুর সোপান
ঢেকে আছে নগ্নযোনি গহরফলক”
(শিল্পের ফলক / লোক লোকান্তর)
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক। কবি আল মাহমুদ আধুনিক কাব্যিক অভিব্যক্তি এবং ছন্দ ব্যবহার করে গ্রাম্যজীবনের অনুপম দৃশ্য এঁকেছেন কবিতায়—যা সত্যিই বিরল। এই বিশেষ স্ট্রেইন (প্রবণতা) থেকে এসেছে তাঁর কিছু সেরা কবিতা, যেগুলো দিয়ে তিনি আরবি ও ফারসি শব্দগুলোকে আরোপিত না করে তাঁর কবিতায় অবিচ্ছেদ্য করে তোলার প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি অন্যতম উদাহরণ হতে পারে। এখানে তিনি তার জন্য নস্টালজিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অন্যান্য কবিতাতেও এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতার সমৃদ্ধ একটি স্ট্রেইন হলো পাঠকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা বা শক্তি। কিছুটা পরাবাস্তবের সঙ্গে বিপুল কল্পনাশক্তি দিয়ে নির্মিত করেছেন কবিতা; যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে একই সময়ে অঞ্চল এবং অঞ্চলগুলিকে অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এই স্ট্রেইনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন দ্বান্দিকতা—নিরীহ এবং পশুত্বের মধ্যে, প্রাচীন এবং ভবিষ্যতের, গ্রাম এবং শহর ইত্যাদি—নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। লোকজ উপাদানের সঙ্গে আধুনিক কল্পনায় নিপুণ সব ছবি এঁকেছেন কবিতায়। বলা যায়, তিনি আধুনিক মোটিফগুলিকে অনন্যভাবে জুতসই করে (যেমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযোজন বা লিবিডো) উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কল্পনার জগতের অনেকাংশ জুড়েই রয়েছে মার্কসবাদী আদর্শের ছায়া।
“সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু’টি”
(সোনালি কাবিন-০১)
“বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত করো কলাবতী/
জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী “
(সোনালি কাবিন-০২)
আল মাহমুদের কবিতায় প্রেম এসেছে নর-নারীর জীবনযাত্রার আলোকে, কখনও শরীরী প্রেমের খোলামেলা প্রকাশে। প্রথম পর্যায়ে আল মাহমুদের কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রয়োগ হয়েছে বিচিত্রভাবে এবং পরিমাণের দিক থেকেও তা অসামান্য। আল মাহমুদের কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রথম দিকে গ্রামের জীবন, বামপন্থী চিন্তা-ধারা এবং নারী মুখ্য হয়ে ওঠে। নদীনির্ভর জনপদ ও প্রকৃতির যে চালচিত্র কবি এঁকেছেন, তা বাংলাদেশের লোকজীবনের এক মৌল অংশ। সোনালি কাবিন-এর চৌদ্দটি সনেটে নারীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত, কবির নিজস্ব প্রেমানুভূতির প্রাধান্য রয়েছে। আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ, মিথ, সাহিত্য প্রভৃতি এবং আবহমান বাঙালি সমাজের নানা বিষয়াদি রয়েছে। তাঁর প্রেম, বিপ্লব এবং ইতিহাস এবং সময়ের ধারণাগুলি সোনালি কাবিন-এ সবচেয়ে শৈল্পিক, পরিণত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অভিব্যক্তি খুঁজে পায়। তিনি শেক্সপিয়রীয় মডেল অনুসরণ করে অসংখ্য শক্তিশালী সনেট লিখেছেন। প্রেম গভীরভাবে নিহিত আছে মাহমুদের। ১৯৭৪ সালের পর আল মাহমুদ তাঁর কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। পূর্বে হিন্দু এবং ইসলামিক উভয় লোকজ এবং ধর্মীয় উপাদানের রেফারেন্সের একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ ছিল, কিন্তু তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বখতিয়ারের ঘোড়া-তে এই আবহের পরিবর্তন আনেন।
“কোথায় সে বালক?
আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফরসালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে ওঠা।”
(বখতিয়ারের ঘোড়া)
“জলজ তুনের মতো ফের
জন্ম নেবে ধরত্রীর মুত্রভেজা যোনীর দেয়ালে।“
(ভারতবর্ষ, বখতিয়ারের ঘোড়া)
তাঁর কবিতার মধ্যে বক্তব্যের চেয়ে সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গির সম্মোহন অনেক বেশি; এর ফলে তাঁর কবিতার অনুবাদও অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশ, বাঙালি, এদেশের আঞ্চলিক শব্দ, লোকাচর, বিভিন্ন মিথ, ধর্ম, কিংবদন্তি সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি এবং প্রখর কবিত্বশক্তি ব্যতীত তাঁর কবিতার ভাষান্তর প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথম কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর (১৯৬৩), দ্বিতীয় কালের কলস (১৯৬৬) এবং তৃতীয় সোনালি কাবিন (১৯৭৩) পর্যন্ত আল মাহমুদের কবিতার একচ্ছত্র অনুষঙ্গ হিসেবে ছিল এই দেশজতা। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো-তে তাঁর কাব্যভাবনা বাঁক নেয় খানিকটা ভিন্ন দিকে।
আল মাহমুদ কবিতায় যে মৌলিকত্ব, ক্ষমতা ও শক্তির সাথে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের লোকসত্ত্বাকে ধারণ করেছেন—তা আর কোনো বাঙালি কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি। লোকজ উপাদান আর জনপ্রিয়তায় আল মাহমুদের ভূমিকা অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। তিনি জীবন উপভোগ করতে চেয়েছেন, নারীর স্বরূপ দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। কল্পনা আর বাস্তবতার মিশ্রণে কবিতাগুলি তাই হয়েছে জীবনময়, গভীরতা পেয়েছে। এ অভিব্যক্তির খোঁজ ও উপলব্ধির প্রকাশে দক্ষতা তাঁর কবিতা গতিময় হয়েছে। তাকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তারপরেও তিনি বাংলা ভাষার দুই ঘর—বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ—উভয়ের কবিতায় প্রিয় ও প্রবল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পঠিত ও আলোচিত হচ্ছেন। কল্পনার উৎস, বিস্তৃতি এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ আল মাহমুদের জনপ্রিয়তায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।


 Reporter Name
Reporter Name